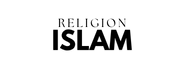প্রিয় ভাই/বোন,
প্রথম সুফিরা তাদের চিন্তা ও অভিজ্ঞতা তাদের চারপাশে জড়ো হওয়া লোকজনের কাছে পৌঁছে দিলেও, আজকের অর্থে কোন তরিকা প্রতিষ্ঠা করেননি। তাদেরকে এবং তাদের চারপাশে জড়ো হওয়া লোকজনকে উস্তাদ বলা হত।
তাসাউউফ মতবাদের একটি ধারা, তাসাউউফ আন্দোলন হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে এমন এই সমষ্টিকরণগুলো, পরবর্তীকালে তরিকা নামে পরিচিতি লাভ করে।
মুহাসিবী (হারিস মুহাসিবী, মৃ. ২৪৩/৮৫৭)
কাসসারিয়ে (হামদুন কাসসার, মৃ. ২৭২/৮৮৪)
তাইফুরিয়া (বায়েজীদ-ই বিস্তাম, মৃ. ২৩৪/৮৪৮)
জুনায়দিয়া (জুনায়দ-ই বাগদাদী, মৃ. ২৯৭/৯০৯)
নূরী (আবু হুসাইন নূরী, মৃ. ২৯৫/৯০৭)
সেহলী (সেহল বিন আবদুল্লাহ তুস্তারী, মৃ. ২৮৩/৮৯৬)
হাকিমিয়া (হাকিম তিরমিযী, মৃ. ২৮৫/৮৯৮)
হাররাজিয়া; (আবু সাঈদ হাররাজ, মৃ. ২৭৭/৮৯০)
হাফিফিয়া (আবু আবদুল্লাহ বিন হাফিফ, মৃ. ৩৭২/৯৮২)
সেয়্যারিয়া (আবু আব্বাস সেয়্যারী, মৃ. ৯৮২)।
বর্তমান ধারার বিচারে, শব্দটি বিবেচনায় নিলে, দেখা যায় যে এটি সুফিবাদের ইতিহাসে দুটি পরিপূরক অর্থ লাভ করেছে।
শিষ্যদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য নির্ধারিত,
এটি একটি মঠ এবং আশ্রমের মধ্যে এবং আশেপাশে সম্মিলিতভাবে বসবাসকারী, একজন পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক নেতার পরিচালনায়, দরবেশদের পরিপূর্ণতা অর্জনের জন্য নির্ধারিত বিশেষ নীতিসমূহের সমষ্টি।
সুফিরা এই লক্ষ্যগুলি অর্জনের জন্য তাদের অনুসারীদেরকে তাদের নিজস্ব আধ্যাত্মিক পদ্ধতি দ্বারা প্রশিক্ষিত করে, একটি নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে আধ্যাত্মিক যাত্রার পদ্ধতি এবং শিষ্টাচার পালন করতেন।
এই রীতি-নীতি এবং আদব-কায়দার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা/গুরু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং প্রয়োগকৃত মূলনীতিসমূহের কাঠামোর মধ্যে অব্যাহত থাকা,
এই সংগঠনগুলো এবং তাদের প্রতিষ্ঠাতাদের প্রতি যে আগ্রহ তৈরি হয়েছে, তার পেছনে সমাজের রাজনৈতিক গোলযোগ, ধর্মীয় বিবাদ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্কেরও ভূমিকা রয়েছে বলে বলা যেতে পারে।
বস্তুত, দশম-একাদশ শতাব্দীতে ইসলামী বিশ্বে বিশৃঙ্খলা, কলহ ও বিবাদ বিরাজ করছিল। এই বিশৃঙ্খলা রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে সমভাবে অনুভূত হচ্ছিল। বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফা এবং নামমাত্র তাদের অনুগত সুলতানদের মধ্যে অবিরাম বিবাদ, ইসলামী মাজহাবসমূহের মধ্যে কলহ, সুন্নি মাজহাবসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতা, অন্তহীন বিতর্কের জন্ম দিচ্ছিল।
রাজনৈতিক অঙ্গনে সংকট, দুর্দশা ও বুদ্ধিবৃত্তিক নৈরাজ্য, জনগণের বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদে ছড়িয়ে পড়া, প্রতিটি দলের গোঁড়ামিতে ঝুঁকে পড়া, জনগণের মধ্যে হতাশা ও নৈরাশ্যের বিস্তার, তাদের মন ভয় ও যন্ত্রণায় ভরে যাওয়া, এবং পরিণামে তাসাউফ (সুফিবাদ) ছাড়া তাদের আর কোন আশ্রয়স্থল না থাকার মত এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছিল।
অপরদিকে, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও ধর্মীয় বিবাদ সুফিদেরকে নিজেদের নীতি প্রচারের সুযোগ করে দিতো এবং ধর্মীয় বিবাদ থেকে দূরে থাকা, নির্জন জীবনযাপন ও ভদ্র আচরণের কারণে জনগণ, রাষ্ট্রনায়ক ও সুলতানরা সুফিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন।
এই পরিস্থিতি সুফিবাদের প্রসারে এবং সুফি সম্প্রদায়ের প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশের দিকে পরিচালিত করে, যা সুফি ধারণার বিস্তারের জন্য এবং প্রথম সুফিদের দ্বারা জোরালোভাবে সমর্থিত এই ব্যক্তিদের ঘিরে জড়ো হওয়া লোকেদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা তৈরি করে।
এভাবে সুফিগণ, চতুর্থ/দশম শতাব্দী থেকে শুরু করে, খানকাহ ও টেক্কেগুলোতে বসতি স্থাপন করতে লাগলেন, যা পঞ্চম/একাদশ শতাব্দীতে ইসলামী বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল।
এই সময়ে সুফিগণ মঠ-জীবনের জন্য এক একটি নির্দিষ্ট নিয়ম প্রণয়ন করেছিলেন এবং সেগুলির প্রত্যেকটিই কোন না কোন প্রসিদ্ধ শেখের দ্বারা পরিচালিত হত।
এই সুফিদের মধ্যে আমরা (মৃত্যু ৪৪০/১০৪৮) কে দেখি, যিনি টেক্কে এবং দরগাহের অনুসারীদের আদব ও পরিচালনার প্রাথমিক নীতিগুলি প্রণয়ন করেছিলেন।
এই ব্যক্তিই সর্বপ্রথম দরবেশ লজের নিয়মকানুন প্রণয়ন করেন, তিনি অনেক দরবেশ লজ পরিচালনা করেন, তার চারপাশে সব জায়গা থেকে অনুসারীরা জড়ো হতেন এবং তিনি সাধারণ মানুষ ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ব্যাপক সম্মান অর্জন করেছিলেন।
এভাবে সুফি আন্দোলন একটি গণমুখী চরিত্র লাভ করে এবং বিভিন্ন তরিকার আকারে সংগঠিত হয়ে, প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিতে কার্যক্রম শুরু করে, জনসমষ্টিকে আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে দিকনির্দেশনা দিয়ে বিকশিত হতে থাকে।
এই বিকাশ ষষ্ঠ/দ্বাদশ শতাব্দীতে একটি সুশৃঙ্খল উপায়ে, আরও নিয়মতান্ত্রিকভাবে দিকনির্দেশনার ক্ষেত্রে একটি শিখরে পৌঁছেছিল।
সেজন্য ষষ্ঠ/দ্বাদশ শতাব্দী এবং তৎপরবর্তী শতাব্দীসমূহকে তাসাউফের তরীকত আকারে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করার যুগ হিসেবে গণ্য করা হয়।
এভাবেই আজকের অর্থে খানকাহ, আশ্রম, শাইখ ও মুরিদ সম্পর্কের মাধ্যমে প্রথম তরিকাগুলো এই শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
বলা যেতে পারে যে, এগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত এবং সংগঠিত হওয়া তরিকাগুলোও বিদ্যমান।
তাসাউফী শৃঙ্খলা, মেজাজ ও স্বভাবের উপযোগী আচার-আচরণ ও পথ অবলম্বনের ঊর্ধ্বে, একটি প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র ধারণকারী একটি কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশকারী প্রথম তরিকা, সাধারণ মতানুসারে, এই তরিকার প্রতিষ্ঠাতা (মৃত্যু ৫৬২/১১৬৬) ছিলেন।
একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত আরেকটি তরিকা হল ‘এটি’। তুর্কি সুফিবাদের ইতিহাসে প্রথম এবং সর্ববৃহৎ প্রভাব বিস্তারকারী এই তরিকার প্রতিষ্ঠাতা হলেন (মৃত্যু ৫৬২/১১৬৬)।
একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত আরেকটি তরিকাও রয়েছে, যা (মৃত্যু: 578/1183) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
১. মাদইয়ানিয়া: আবু মাদইয়ান শুয়াইব ইবনে হুসাইন (মৃত্যু ৫৯০/১১৯৩)।
২. কুবরাবিয়া: নাজমুদ্দিন কুবরা (মৃত্যু ৬১৮/১২৩৬)।
৩. সুহরাওয়ার্দিয়া: আবু হাফস ওমর আস-সুহরাওয়ার্দী (মৃত্যু ৬৩২/১২৩৬)।
৪. চিশতিয়া: মুঈনুদ্দীন হাসান আল-চিশতি (মৃত্যু ৬৩৩/১২৩৬)।
৫. একবরিয়্যা: মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (মৃত্যু ৬৩৮/১২৪০)।
৬. শাজেলিয়া: আবু’ল-হাসান আশ-শাজেলি (মৃত্যু ৬৫৬/১২৫৮)।
৭. বেক্তাশি সম্প্রদায়: হাজী বেক্তাশ-ই-ভেলি (মৃত্যু ৬৬৯/১২৭০)।
৮. মৌলভীয়া: মাওলানা জালালুদ্দিন রুমী (মৃত্যু ৬৭২/১২৭৩)।
৯. বেদবিয়্যা: আহমদ বিন আলী বেদবী (মৃত্যু: ৬৭৫/১২৭৬)।
10. দিসূকিয়্যা: ইব্রাহিম বুরহানুদ্দিন আদ-দিসূকী (মৃত্যু: ৬৯৩/১২৯৫)।
১১. সা’দিয়্যা: সা’দুদ্দীন বিন মূসা জিবাবী (মৃত্যু: ৭০০/১৩০)।
১২. হালভেতিয়া: ওমর ইবনে একমালুদ্দিন হালভেতি আল-লাহিজি (মৃত্যু: ৭৫০/১৩৮৯)।
১৩. নকশবন্দী তরিকা: বাহাউদ্দীন নকশবন্দী (মৃত্যু: ৭৯১/১৩৮৯)।
১৪. বায়রামীয়া: হাজী বায়রাম-ই-ভেলি (মৃত্যু: ৮৩৩/১৪৩০)
১৫. জালভেতিয়্যা: আযীয মাহমুদ হুদায়ী (মৃত্যু: ১০৩৮/১৬২৮)।
এই সমস্যার দুটি দিক রয়েছে।
যদি আমরা একটি তরিকার প্রাথমিক গঠন প্রক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নটির উত্তর দিই, তাহলে সাধারণভাবে, তরিকার প্রতিষ্ঠাতা ব্যক্তি নিজেও একটি তরিকা প্রতিষ্ঠা করছেন তা বুঝতে পারেন না। তরিকাগুলি সমাজে স্বাভাবিক/প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রথমে গঠিত হতে শুরু করে, কালক্রমে একজন কামিল মুর্শিদের চারপাশে মানুষের সমাগমের ফলে সামাজিক গোষ্ঠী গঠিত হয়। পরবর্তী ধাপে, সমাজ এই সামাজিক গোষ্ঠীগুলিকে একটি নাম দেয়।
উদাহরণস্বরূপ, আব্দুলকাদির জিলানীর আলোচনা চক্রের চারপাশে জড়ো হওয়া লোকেদেরকে আব্দুলকাদির জিলানীর অনুসারী অর্থে নাম দেওয়া হয়।
এভাবেই তরিকার প্রথম প্রতিষ্ঠাতারা নিজেদেরকে শায়খ হিসেবে ঘোষণা করেন না, বরং মানুষই তাদেরকে শায়খ হিসেবে দেখে।
সমস্যার অপর দিকটি হল, একটি সুগঠিত তরিকার শেখের মৃত্যু হলে, তার স্থলাভিষিক্ত খলিফা, যদি খলিফা নিযুক্ত না থাকে, তাহলে সেই পদের জন্য যোগ্য বিবেচিত কেউ শেখের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং শেখের দায়িত্ব গ্রহণের কথা জনগণকে জানানোর জন্য নিজেকে শেখ হিসেবে ঘোষণা করে। এভাবে ভুয়া শেখদের উত্থানও রোধ করা হয়।
(মৃত্যু: ১৫০/৭৬৭)
‘এর মৃত্যুর তারিখটি বিবেচনায় নিলে, আমরা বলতে পারি যে, তিনি যে সময়ে বাস করতেন, সেই সময়ে আজকের পরিচিত বড় তরিকাগুলো তখনও অস্তিত্বে ছিল না, এ কারণে তিনি কোনো পরিচিত তরিকার অনুসারী ছিলেন না।
তবে ইমাম-ই আজমের শিক্ষকদের মধ্যে জাফর-ই সাদিকও রয়েছেন। জাফর-ই সাদিক অনেক তরিকার সিলসিলায় গুরুত্বপূর্ণ একটি নাম।
আনুষ্ঠানিকভাবে তরিকাগুলো দ্বাদশ শতাব্দীর পর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই শতাব্দীর পূর্ববর্তী সময়ে সুফিবাদ ব্যক্তিগতভাবে চর্চা ও পালন করা হত। জাফর-ই-সাদিক কোন তরিকার শেখ নন, তবে একজন গুরুত্বপূর্ণ সুফি। ইমাম-ই-আজমেরও তাঁর কাছ থেকে সুফি তত্ত্বের জ্ঞান লাভ করার সম্ভাবনা রয়েছে।
(মৃত্যু: ৫০৫/১১১১)।
ইমাম-ই-আজমের ক্ষেত্রেও আমরা যে যুক্তি দিয়েছি তা প্রযোজ্য। প্রথম বড় তরিকাগুলো গজালী থেকে প্রায় এক শতাব্দী পরে গঠিত হবে। তাই গজালী পরিচিত বড় তরিকাগুলোর কোনোটিরই অনুসারী নন। তবে তিনি একজন সুফি ছিলেন এবং আবু আলী আল-ফারমেদী নামক এক সুফির কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেছিলেন।
গাজ্জালী তাঁর রচনায় স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন যে, তিনি কালাম ও দর্শন শাস্ত্রের চর্চা করেও তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেননি, অতঃপর তিনি তাসাউফের দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং এখানেই তিনি তাঁর কাঙ্ক্ষিত সত্যকে খুঁজে পান। তাসাউফের দিকে ঝুঁকে পড়ার পর এবং কার্যত সূফী জীবন যাপন শুরু করার পর তিনি নির্জনবাসে চলে যান এবং দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে আত্মশুদ্ধির কাজে নিয়োজিত থাকেন।
এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বলা যায় যে, গাজ্জালী চল্লিশ বছর বয়সে সুফিবাদের দিকে ঝুঁকেছিলেন এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি এখানেই সেই সত্যকে খুঁজে পেয়েছেন বলে বিশ্বাস করে জীবন কাটিয়েছেন।
তবে, তার সুফিবাদ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও আগ্রহ শৈশব থেকেই শুরু হয়েছিল। গাজ্জালীর পিতা মুহাম্মদ ছিলেন ধর্মপ্রাণ ও সংবেদনশীল ব্যক্তি, যিনি ধর্মীয় উপদেশ সভায় আগ্রহী ছিলেন। মৃত্যুর সময় তিনি তার দুই নাবালক পুত্র মুহাম্মদ ও আহমদের শিক্ষার ভার তার এক সুফি বন্ধুর কাছে অর্পণ করেছিলেন। সূত্রগুলো উল্লেখ করে যে, এই সুফি ব্যক্তি ছিলেন ফকির ও নির্জনবাসী।
আব্দুল করিম আল-কুশাইরির ছাত্র এবং আবুল কাসিম আল-জুরজানির অনুসারী আবু আলী আল-ফারমেদী (মৃত্যু ৪৭৭/১০৮৪) কে কিছু সূত্রে গাজ্জালীর শায়খ হিসেবে গণ্য করা হয়। এ থেকে বোঝা যায় যে গাজ্জালী সাতাশ বছর বয়সের আগেই সুফি জীবনের প্রতি গভীর আগ্রহ পোষণ করতেন। গাজ্জালী নিজেই ফারমেদীর সান্নিধ্যে থাকার কথা উল্লেখ করেছেন।
সংক্ষেপে, ৫ম/১১শ শতাব্দীতে জীবিত থাকা তাঁর দ্বারা বিকশিত ও সু systematized আহলে সুন্নাত তাসাউউফ, পরবর্তীতে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিতে কার্যক্রম শুরু করে।
সালাম ও দোয়ার সহিত…
প্রশ্নোত্তরে ইসলাম