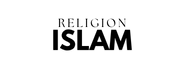প্রিয় ভাই/বোন,
“জ্বালা” শব্দটি আরবি মূল থেকে এসেছে, যার অর্থ উজ্জ্বল আগুন, দীপ্তি এবং তীক্ষ্ণতা।
মানুষের নিজের এবং তার চারপাশের মহাবিশ্বকে পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উপলব্ধি ও অর্থবহ করে তোলা বুদ্ধিমত্তার দ্বারাই সম্ভব। নতুন পরিস্থিতি ও ঘটনায় উপনীত হওয়া, বোঝা, শেখা, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করার ক্ষমতা, পঞ্চেন্দ্রিয় ও অন্তর্দৃষ্টির একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় ব্যবহার, মনোযোগ ও চিন্তার একাগ্রতা, খুঁটিনাটির প্রতি দৃষ্টিপাত বুদ্ধিমত্তার উপস্থিতির দ্বারাই সম্ভব।
মানব বুদ্ধিমত্তা, মানব আত্মার ছত্রছায়ায় চেতনা, বুদ্ধি, বিবেক, অন্তর্দৃষ্টি, অনুভূতি এবং স্মৃতির মতো অনুষদগুলির প্রত্যেকটির সাথে একযোগে কাজ করে। এই অবিচ্ছেদ্য একতার কারণে, হ্রাসকারী বা বিমূর্ত পদ্ধতির মাধ্যমে মানব বুদ্ধিমত্তাকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। মানব বুদ্ধিমত্তার, মানুষের সত্তার অন্যান্য আধ্যাত্মিক অনুষদের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকা, আমাদের এই সিদ্ধান্তে নিয়ে যায় যে বুদ্ধিমত্তার একটিমাত্র সংজ্ঞা থাকতে পারে না এবং মানব বুদ্ধিমত্তা, পশুর বুদ্ধিমত্তা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদির মতো বিভিন্ন বুদ্ধিমত্তার সংজ্ঞা তৈরি করা আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় করে তোলে। এছাড়াও, মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার মধ্যে একটি শক্তিশালী সম্পর্ক থাকায়, বিভিন্ন ধরনের বুদ্ধিমত্তার কথাও বলা যেতে পারে।
অন্যদিকে, প্রত্যেকটি প্রাণ ও বুদ্ধিসম্পন্ন সত্তা একইসাথে চেতনা ও যুক্তির অধিকারী নাও হতে পারে। প্রাণীরা, নিজেদের মধ্যে ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও, একটি নির্দিষ্ট বুদ্ধির স্তরের অধিকারী, কিন্তু যুক্তির অভাব রয়েছে; সুতরাং, তাদের বুদ্ধিমত্তা অবশ্যই মানুষের বুদ্ধিমত্তা থেকে আলাদা।
শিখন বলতে যদি কিছু থাকে, তবে তা হল, প্রাণীটি আগে যে গন্ধ, স্বাদ, বস্তু বা গতির সম্মুখীন হয়েছিল, তার সাথে পুনরায় সম্মুখীন হলে একটি প্রতিবর্ত ক্রিয়া হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করে, বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির মাধ্যমে নয়। অতএব, প্রাণীর স্মৃতি মানুষের স্মৃতি থেকে আলাদা। মানুষের স্মৃতি তার আত্মার অন্যান্য অনুষদের সাথে জটিলভাবে যুক্ত। তথ্য স্মৃতিতে আসে বুদ্ধিমত্তা, অনুভূতি, অন্তর্দৃষ্টি, বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি এবং ইচ্ছার মাধ্যমে। যে তথ্যগুলি আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় না, সেগুলি স্মৃতিতে প্রবেশ করে না। কারণ আমরা তাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিই না। উদাহরণস্বরূপ, যদি আমাদের কোন বন্ধুর সাথে প্রথমবার দেখা হওয়া কোন ব্যক্তি আমাদের কাছে কোন অর্থ বহন না করে, তাহলে তাকে নাম ধরে পরিচয় করিয়ে দিলেও আমরা সাধারণত তার নাম তৎক্ষণাৎ ভুলে যাই। কিন্তু বিভিন্ন কারণে যদি আমরা তার নাম জানতে চাই, তাহলে তা আমাদের স্মৃতিতে যত্ন সহকারে লিপিবদ্ধ হয়। পরিশেষে, আমরা বলতে পারি যে মানুষের গঠন ও কার্যকারিতার দিক থেকে একটি অনন্য বুদ্ধিমত্তা একক রয়েছে।
বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশক্তির মধ্যে, এবং চিন্তাশক্তি ও ব্যক্তির মানসিক গঠন (বা ব্যক্তিত্ব) এর মধ্যে একটি দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে। দেখা গেছে যে, খুব বুদ্ধিমান হওয়া সত্ত্বেও, শৈশবকাল থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার নেতিবাচক প্রভাবের কারণে, যারা সামাজিক হতে পারেনি, লাজুক ও ভীরু থেকে গেছে, এবং আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভোগে, তারা স্বতঃস্ফূর্ত ও বাধাহীন চিন্তা বিকশিত করতে পারে না, ফলে তাদের বুদ্ধিমত্তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারে না। এ বিষয়ে আইনস্টাইনের শৈশবকাল একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ:
স্কুলে তাকে তার নামের অর্থবোধক একটি ডাকনাম দেওয়া হয়েছিল। কোনো প্রশ্নের উত্তরে ভুল কিছু না বলার জন্য, সে অনেকক্ষণ ভেবে উত্তর দিত। এমনকি একসময় তার বুদ্ধিমত্তার ঘাটতি নিয়ে পরিবারে আশঙ্কাও দেখা দিয়েছিল। স্কুলে তার অবস্থা নিয়ে তার মা, এক আত্মীয়কে লেখা চিঠিতে এই কথাগুলো উল্লেখ করেছিলেন। এই অবস্থাটা আইনস্টাইনের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ক্যাথলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, যেখানে একটা চাপের পরিবেশ বিরাজ করত, সেখানে হওয়ার কারণেই হয়েছিল। আইনস্টাইন তার স্মৃতিকথায় স্কুলের শিক্ষকদের আচরণের কথা উল্লেখ করবেন, এবং বলবেন যে শিক্ষকরা কেমন আচরণ করতেন।
এই উদাহরণের মতো, একজন ব্যক্তি, তার ব্যক্তিত্বের ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া বা সুস্থ বিকাশের সুযোগ না পাওয়ার মতো পরিস্থিতিতে, যতই বুদ্ধিমান হোক না কেন, এই সমস্যার সমাধান করতে নাও পারতে পারে। এখানে, মানুষের আদর্শের অধিকারী হওয়া তার ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করবে, তার আত্মবিশ্বাসকে বাড়াবে, পরিণামে সে নিজেকে আরও স্বাধীন এবং স্বাচ্ছন্দ্যে প্রকাশ করতে পারবে।
উপরের পরিস্থিতির ঠিক উল্টোটাও দেখা যেতে পারে। কিছু লোক অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী এবং বিক্ষিপ্ত চিন্তার অধিকারী, তারা জোরালো বিশ্লেষণ করতে পারলেও, সংশ্লেষণাত্মক চিন্তার প্রতি আগ্রহ বা ধৈর্য দেখাতে পারে না। এরা সাধারণত জীবনে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর কথা ভাবে না। এরা সমালোচনামূলকভাবে কথা বলে। এতে তাদের উচ্চ মনোযোগ, জন্মগত স্বভাব ও মেজাজ এবং লালন-পালনের ভূমিকা রয়েছে। অন্যদিকে, বুদ্ধিমান হওয়া সত্ত্বেও যারা ক্রমাগত অসঙ্গতি প্রদর্শন করে, যাদের কাজকর্ম বুদ্ধিমানের মতো নয়, তা তাদের আত্মবিশ্বাসের দুর্বলতার কারণে হতে পারে।
কিছু মানুষ দ্রুত চিন্তা করার, দ্রুত তথ্য মূল্যায়ন করে নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করার, তা থেকে নতুন ধারণা বিকাশ করার, দ্রুত বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করার ক্ষমতা রাখে। উচ্চ বোধগম্যতা ও উপলব্ধি ক্ষমতা সম্পন্ন, দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারা, সতত জাগ্রত মনোযোগ ও কৌতূহল বিশিষ্ট মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে স্বাভাবিক গতিতে পরিচালিত শিক্ষা/প্রশিক্ষণে তাল মেলাতে না পারা, এই গতির পার্থক্যের কারণে তাদের বিরক্ত হওয়ার কারণেই। এই ব্যক্তিরা তাদের দ্রুতগামী চিন্তাকে একই গতিতে লিখে প্রকাশ করতে না পারায়, সাধারণত কথা বলতে পছন্দ করে। কারণ তাদের চিন্তার প্রক্রিয়া কলম ধরা হাতের চেয়ে দ্রুত কাজ করে। লেখালেখির কাজ গতি কমিয়ে দেয়; ফলে হোঁচট খাওয়া, বাদ পড়া, ভুলে যাওয়া এবং পরে মনে পড়া হতে পারে, যা প্রেরিত তথ্যের ধারায় ত্রুটিপূর্ণ ক্রমবিন্যাস, স্থান পরিবর্তন ঘটাতে পারে এবং উদ্দেশ্যটি কাঙ্ক্ষিত উপায়ে প্রকাশ নাও হতে পারে। সতত ব্যস্ত মনোযোগ ও আগ্রহ বিশিষ্ট, অপ্রয়োজনীয়ভাবে সময় নষ্ট করতে বিরক্ত হওয়া এই ব্যক্তিদের লেখা খুব সুশৃঙ্খল নাও হতে পারে।
এর একটি উদাহরণ হল, বদিউজ্জামান, যিনি ঠিকমতো লিখতে পারতেন না, নিজেকে অর্ধ-নিরক্ষর হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর এই বৈশিষ্ট্যটি তাঁর রচনাগুলিকে, যা তাঁর অন্তরে প্রেরণার মাধ্যমে আসত এবং তাঁর মুখ থেকে দ্রুত উচ্চারিত হত, তাঁর ছাত্রদের দ্বারা লিপিবদ্ধ করানোর প্রয়োজনীয়তা তৈরি করেছিল। এই ধরনের সৃষ্টিশীল ব্যক্তিরা, তাদের বহুমুখী মন থেকে আসা উজ্জ্বল সত্যের অভিব্যক্তিগুলিকে ছোট নোট আকারে লিখতেও পছন্দ করতে পারেন। তাঁর নামকৃত গ্রন্থটি এর একটি সুন্দর উদাহরণ।
আবার কারো কারো ক্ষেত্রে এই রূপান্তর দ্রুত হয় না। বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণের ক্ষমতা একই গভীরতার হলেও, তারা স্বভাবগত কারণে নতুন পরিস্থিতিতে আরও সতর্কতার সাথে, ধীর-স্থিরভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রবণতা দেখায়। তাদের জন্য তথ্যকে লিখিত আকারে প্রকাশ করা বেশি উপযোগী হতে পারে। এক্ষেত্রে ধৈর্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ধৈর্যশীল হলে, প্রথম দলের মতো তারাও সুন্দর লেখা লিখতে পারে। পাঠক এই লেখাগুলো এমনভাবে পড়বে যেন সে তাদের কথা শুনছে।
আরবি অভিধানে ‘আক্বল’ শব্দের বিভিন্ন অর্থ রয়েছে, যার একটি অর্থ হল ‘বন্ধন’। এখানে ‘বন্ধন’ বলতে বোঝায় দুটি বস্তুর বা দুটি ধারণার মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ সংযোগ স্থাপন করা। যেমন, কলম ও লেখা শব্দের মধ্যে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সংযোগ (সম্পর্ক) রয়েছে: এইভাবেই, প্রস্তাবটি যুক্তিসঙ্গত।
বুদ্ধি ও মনের প্রকৃতি ও কার্যকারিতা ভিন্ন। মন প্রজ্ঞার জন্য। চিন্তা করা, যুক্তি করা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। গ্রহণকারী বা অগ্রহণকারী, অর্থাৎ সিদ্ধান্ত, পছন্দ ও নির্বাচনকারী হল মন। কারণ মন একইসাথে ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন। বুদ্ধি ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন নয়, এবং কেবল মনের কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে। পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে, এবং অন্তর্দৃষ্টি ও অনুভূতির মাধ্যমে মানুষের চেতনায় প্রবাহিত তথ্যকে সে গ্রহণ করে এবং মনের সামনে উপস্থাপন করে। এদের ইচ্ছাকৃত, বিষয়গত মূল্যায়ন মন করে। এভাবে মানুষ তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও পছন্দ, তার মানসিক কার্যাবলীর মাধ্যমে নির্ধারণ করে। এটি একইসাথে মানুষের ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ। বুদ্ধিমান হওয়ার জন্য বুদ্ধি একটি স্বাভাবিক পূর্বশর্ত হলেও, বুদ্ধিমান হওয়ার জন্য মন থাকা কোন পূর্বশর্ত নয়। এমন তুলনা সঠিক নয়, কারণ মন মানুষের মনন ও চিন্তার কার্যে পরবর্তী পর্যায় গঠন করে।
বুদ্ধি হল মনের ব্যবহার করার জন্য প্রদত্ত একটি ইঞ্জিন, আর এই ইঞ্জিনের দক্ষ ও ফলপ্রসূ ব্যবহার মনের কার্যকারিতার মাধ্যমেই সম্ভব। অন্যথায়, শুধু ধূর্ততা অবশিষ্ট থাকে। খুব বুদ্ধিমান, বা বলা যায় খুব ধূর্ত চোরের কথা বলা যেতে পারে, কিন্তু তাকে কখনো বুদ্ধিমান বলা যায় না। কারণ সে ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে পারেনি এবং নিজেকে এক বিপথগামী পথে ঠেলে দিয়েছে। অবৈধ উপার্জন সারা জীবন তার বিবেককে পীড়া দেবে।
একটি গাড়ির সাথে তুলনা করলে, বুদ্ধিকে ইঞ্জিনের সাথে এবং মনকে স্টিয়ারিং হুইলের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। ইঞ্জিন খুব ভালো কাজ করতে পারে, কিন্তু যদি স্টিয়ারিং হুইল ঠিকমতো ব্যবহার না করা হয়, তাহলে ইঞ্জিনের কার্যকারিতা কোন কাজে আসবে না। গাড়ি যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। পরিশেষে, চিন্তার ক্রিয়া, যা যৌক্তিক বিচারের পূর্ববর্তী ক্রিয়া, বুদ্ধির অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু, এর অর্থ এই নয় যে, যে কেউ চিন্তা করে সে তার মনকে ব্যবহার করছে।
যদি আমরা মানববুদ্ধিকে মহাবিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফল হিসেবে ধরি, তাহলে বুদ্ধির স্রষ্টাকে জানাটাই হতে পারে তার চূড়ান্ত অস্তিত্বের কারণ; বুদ্ধির অন্যান্য সমস্ত ক্রিয়াকলাপও এই ফলাফল অর্জনের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ। বুদ্ধি মহাবিশ্বকে অন্বেষণ করবে, মানুষ নামক ব্যতিক্রমী সত্তাকে চিনবে এবং এই সবই তাকে তার স্রষ্টার কাছে নিয়ে যাবে। অতি বুদ্ধিমান হওয়া সত্ত্বেও যারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি, অর্থাৎ যারা তাদের বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে পারেনি বা জন্মগতভাবে প্রাপ্ত বুদ্ধির সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপান্তর করতে পারেনি (বিজ্ঞানী, দার্শনিক), তারা চলে গেছে। এখানে আমরা এক অর্থে দর্শন-প্রজ্ঞার পার্থক্যও দেখতে পাই: দর্শন, যা এক ধরনের বুদ্ধির খেলা যা ক্রমাগত বিশ্লেষণাত্মক থাকতে বাধ্য, এবং প্রজ্ঞা, যা বুদ্ধির যুক্তির মাধ্যমে অর্জিত হয়, এই দুটির মধ্যে পার্থক্য। বেদীউজ্জামান কোরআনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করার সময় এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন:
“উদাহরণস্বরূপ, কোরআন সূর্যের কথা বলে: কারণ কোরআন সূর্য থেকে, সূর্যের জন্য, সূর্যের সারবস্তু নিয়ে আলোচনা করে না, বরং একপ্রকার শৃঙ্খলা ও নিয়মের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে; আর শৃঙ্খলা ও নিয়ম হল স্রষ্টার জ্ঞানের আয়না। হ্যাঁ, এই উক্তির মাধ্যমে; শীত, গ্রীষ্ম, রাত, দিনের আবর্তনের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা স্মরণ করিয়ে দিয়ে, স্রষ্টার মহিমা বুঝিয়ে দেয়…”
এই বোকা আর বাচাল দর্শন কী বলে? দেখো, সে বলে:
মানব বুদ্ধিমত্তার বর্তমান স্তর হল, বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ফলাফলের মাধ্যমে অস্তিত্বের জগতকে অত্যন্ত বিশদভাবে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করতে পারা। কিন্তু এক ধাপ এগিয়ে এই অস্তিত্বের অলৌকিকতার পেছনের জ্ঞান ও শক্তিকে দেখতে পারা, তা কেবল বুদ্ধির কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করে, বুদ্ধির ব্যবহারের মাধ্যমেই সম্ভব (ভাগ্যের দিক থেকেও এটি একটি নিয়তির বিষয়)। অর্থাৎ, শুধু বুদ্ধিমত্তা যথেষ্ট নয়। কুরআনের,
এইসব আয়াত বুদ্ধির কার্যক্ষেত্রের ঊর্ধ্বে, কিন্তু বিবেকের প্রাপ্য এবং মানুষকে প্রজ্ঞার দিকে নিয়ে যাওয়া এই বোধগম্যতা, এই চিন্তাশীলতা, এই যুক্তিকে তুলে ধরে। তাই কোরআন বলে, বলে না। কারণ বুদ্ধি, বিবেকের জন্য কেবল একটি পূর্বশর্ত। বুদ্ধি না থাকলে বিবেকই নেই। চূড়ান্ত লক্ষ্য বিবেক। কোরআন বিবেককে সম্বোধন করে। কারণ বোধগম্যতা ও যুক্তি, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও পছন্দ বিবেক দ্বারাই হবে। তাই বলা যেতে পারে যে, কোরআনী অর্থে চিন্তাশীলতা হল বুদ্ধির সত্যের অন্বেষণ, নিজেকে সবচেয়ে সঠিক উপায়ে, সবচেয়ে সঠিক স্থানে ব্যবহার করা এবং চিন্তাশীলতা নামক ঘটনারই স্বরূপ। এমন বিবেক, বুদ্ধির ক্রিয়াকলাপ দ্বারা সংগৃহীত তথ্যের পেছনের প্রজ্ঞাকে দেখে, অর্থাৎ কেবল শুষ্ক তথ্যের স্তরেই থাকে না; একটি উচ্চতর অনুষদ হিসাবে কার্য করে। বুদ্ধি সত্য ও দৃশ্যমান বাস্তবতাকে, আর বিবেক সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ তাদের ক্ষেত্র ভিন্ন। এভাবে, কেবল তারাই যারা সত্যকে অন্বেষণ ও খুঁজে পাওয়ার অভিপ্রায় রাখে, তারাই তা অর্জন করতে পারে, সত্যের উপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
সত্যকে মিথ্যা থেকে, ভালকে মন্দ থেকে, সঠিককে ভুল থেকে বিবেক দিয়ে আলাদা করা যায়, বুদ্ধিমত্তা দিয়ে নয়। বুদ্ধিমত্তা বাস্তবতা নির্ণয় করে, আর বিবেক সেই নির্ণয়কে ব্যক্তির অভিপ্রায় অনুযায়ী ব্যাখ্যা করে এবং নিজের মতো করে একটা জায়গায় বসিয়ে দেয়। বিবেক যদি অনুভূতির আগে রাখা যায়, তাহলে সুস্থ বিচার করা যায়। যারা এটা করতে পারে, তাদের কাছে সত্য একটাই, অপরিবর্তনীয়। অন্যথায়, যতজন মানুষ ততটা সত্য সামনে আসে। তাই বলা হয়েছে। বিবেককে কাজে লাগাতে না পারাটা সাধারণত প্রবৃত্তির ও অনুভূতির দ্বারা তার সামনে পর্দা পড়ে যাওয়ার কারণেই হয়। এটা পূর্বধারণা, শর্তাধীনতা এবং প্রবৃত্তিমূলক, আবেগপ্রবণ প্রতিক্রিয়ারূপে প্রকাশ পায়। আর অনুভূতি হৃদয়ের সাথে সম্পর্কিত। কোরআন, অকালপক্ব, অসুস্থ ও বিপথগামী হৃদয়ের কথা বলে। এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, হৃদয়েও একটা চেতনার গুণ থাকতে পারে।
পরবর্তীটা ব্যক্তির অভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করে এবং সে অনুযায়ী রূপ নেয়। বদিউজ্জামান বলেন যে, তিনি জীবনে চারটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যে উপনীত হয়েছেন; তার মধ্যে একটি হল অভিপ্রায়। অভিপ্রায় আসলে হৃদয়ের ঝোঁক এবং এটি বুদ্ধিবৃত্তিক বিচারের দিক ও ফলাফল নির্ধারণ করে। অর্থাৎ, যদি ব্যক্তির অভিপ্রায় সত্যের অন্বেষণ না হয়, তাহলে যা বোঝাতে চাওয়া হচ্ছে তা হল বুদ্ধিবৃত্তিক বিচারের স্থবিরতা। এমন অবস্থায়, ব্যক্তির অতি বুদ্ধিমান হওয়া সত্যের খাতিরে তাকে কিছুই এনে দেবে না।
সালাম ও দোয়ার সহিত…
প্রশ্নোত্তরে ইসলাম